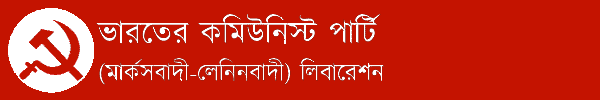২০০৯ সালে এল শিক্ষার অধিকার আইন। আট থেকে চোদ্দ বছর পর্যন্ত সবার জন্য। ফেল থাকলো না ক্লাস এইট অবধি। স্কুলে ভর্তির জন্যও কোনও পরীক্ষা, মেধাতালিকা তৈরি করা ইত্যাদি বাদ দিয়ে দেওয়া হল।
এর ফলে নিঃসন্দেহে বেশ কয়েকটি সুবিধে হল। যে সমস্ত প্রান্তিক পরিবারের ছাত্র ছাত্রীরা আগে সাধারণভাবে স্কুলের চৌহদ্দিতে আসত না, বা এলেও খুব সামান্য দিন পর স্কুল ছুট হয়ে যেত, তারা স্কুলে থেকে গেল। অন্তত খাতায় কলমে থেকে গেল। কেউ কেউ পড়াশুনো সামান্য শিখলও মাঝে মাঝে স্কুলে এসে। আর ব্যতিক্রমী কয়েকজন অনেকদূর এগিয়ে গেল। আগেই চালু হয়েছিল মিড ডে মিল প্রকল্প। সেটাও প্রান্তিক পরিবারের কিছু ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে ধরে রাখতে সাহায্য করল।
কিন্তু এই যে সাফল্যটা, এর কিছু মূল্যও দিতে হল। কী ধরনের মূল্য? সরকারী স্কুলগুলি, বিশেষ করে শহর শহরতলীতে খুব দ্রুত মধ্যবিত্ত পরিবারের কাছে ব্রাত্য হয়ে গেল। অল্প কয়েকটি সরকারী স্কুল বাদ দিয়ে বাকিগুলিতে প্রান্তিক পরিবারের ছেলেমেয়েরাই কেবল ভর্তি হলেন। যাদের কিছু টাকা পয়সা আছে তারা বেসরকারী ইংরাজি মাধ্যম স্কুলে চলে গেলেও সেই মাত্রায় সমস্যা ছিল না, যদি সরকারী স্কুলগুলোর গুণমান বজায় থাকত। তাহলে অভিভাবক অভিভাবিকা, এমনকী যারা আর্থিকভাবে বেশ সবল, তারাও ইচ্ছে হলে সরকারী স্কুলগুলোতে তাদের ছেলেমেয়েদের পড়াতে পারতেন। কিন্তু অবস্থা এমনই দাঁড়াল যে সরকারী স্কুলগুলো মূলত ৮০/৯০ শতাংশ এমন ছাত্রছাত্রীতে ভরে থাকল যাদের বইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ খুব ক্ষীণ বা সামান্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও ফেল প্রথা না থাকায় তারা পরের পর ক্লাসে উঠে যেতে থাকল। ফলে ক্লাসরুমে দেখা যেতে লাগল এমন সব ছেলেমেয়েকে যারা সেই ক্লাসের পড়া খুব সহজ করে বুঝিয়ে বললেও সেটা বোঝার জায়গায় থাকল না। সেই সঙ্গে স্কুলে খুব অনিয়মিত হওয়ায় পাঠের ধারাবাহিকতা থেকেও তারা থাকল বিচ্ছিন্ন।
গোটা বিষয়টিকে একটা সমস্যা, যার জরুরি সমাধান হিসেবে দেখা প্রয়োজন, সেইভাবে দেখা হল না। দেখা হল কেবল ওপর ওপর একটা ‘মানবিক সহনাভূতি’র সঙ্গে। আহা গরিব, বাড়িতে পড়াশুনোর পরিবেশ নেই, পড়বে কী করে’ – এই কথা বলে তাদেরও যে সুশিক্ষার একটা দরকার ছিল, সেটা কীভাবে তাদের দেওয়া যায়, সেটাকেই লঘু করে দেওয়া হল। তাদের প্রতি আপাত সহানুভূতি দেখিয়ে আসলে তাদের ক্ষতি করে দেওয়া হল মারাত্মকভাবে। দরকার ছিল তাদের প্রতি প্রকৃত সহানুভূতি। সেটা তাদের জন্য সুশিক্ষা নিশ্চিত করার মধ্যে দিয়েই হতে পারত।
এরই সঙ্গে কিছু বাকপটু বুদ্ধিজীবী কিছু কিছু কথা তুলতে লাগলেন যা তাত্ত্বিকভাবে যতই মনোহর শোনাক, কার্যক্ষেত্রে একেবারেই অকার্যকরী। যেমন তারা বললেন ছাত্রকে ফেল করানো ঠিক নয়। কারণ ছাত্র যদি শিখতে না পারে তাহলে তা ছাত্রের নয়, শিক্ষকেরই ব্যর্থতা। সিস্টেমের সমস্যা আড়াল করে সব দায় শিক্ষকের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার কথাটা শুনতে কারো কারো যতই ভালো লাগুক, ক্লাসঘরের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যারা নিত্যদিন যান, তারা বাস্তবে জানেন কথাটার মধ্যে আর যাই থাক, বাস্তবতা নেই। সত্যকে আড়াল করার একটা চেষ্টা আছে। যে ছেলেটি বা মেয়েটি শিখতে পারছে নানা কারণেই, যে আগের নিচু ক্লাসগুলোতে পাশ না করে করে পরের পর উঁচু ক্লাসগুলোতে এসে বসেছে, তাকে যে উঁচু ক্লাসের পড়াটা শেখানো সম্ভব নয় – শিক্ষাবিজ্ঞানের এই অ আ ক খ ভুলে যাওয়ার কোনও মানেই হয় না। প্রথম বিশ্বের নানা দেশে যে মডেল চলে, তৃতীয় বিশ্বের প্রান্তিক পরিবারে ছেয়ে থাকা দেশে বা রাজ্যে সেই মডেল কিছুতেই চলতে পারে না। আমাদের দেশ বা রাজ্যের সমস্যা আমাদের নিজস্ব। এখানকার পরিস্থিতি অনুযায়ীই এখানকার নীতিমালা স্থির করতে হবে।

আমাদের এখানে দিনের পর দিন সবচেয়ে অবহেলিত প্রাথমিক স্তরের স্কুলশিক্ষা। অথচ প্রাইমারি স্কুলশিক্ষার ওপরে মারাত্মক জোর না দিয়ে কিছুই করা যাবে না। কারণ সেটি ভিত তৈরির জায়গা। আমাদের এখানে প্রাইমারি স্কুলগুলোর অবস্থা দেখুন। পড়াশুনো অধিকাংশ জায়গাতে নামে মাত্র। পাশ ফেল প্রাইমারিতে বহুদিন ধরেই নেই। প্রাইমারিতে শুরুতেই ফেল থাকাটা হয়ত দরকারও নেই। কিছুটা সময় একটি শিশুকে নির্ভয়ভাবে স্কুলে খাপ খাওয়ানোর জন্য দেওয়াই উচিত। কিন্তু ক্লাস ফোর থেকে একটি ছেলেকে কেন প্রাইমারি পাশ সার্টিফিকেট দিয়ে হাইস্কুলে পাঠিয়ে দেওয়া হবে, যে বাংলা বর্ণমালা ভালো চেনে না, যুক্ত অক্ষর পড়তে পারে না, একটি সহজ বাক্য পড়তে পারে না ? এইভাবে পাশের পরিসংখ্যান তৈরি করে লাভ কি ?
পশ্চিমবঙ্গের স্কুল শিক্ষার ভয়ানক চিত্রটি বিভিন্ন সমীক্ষার রিপোর্ট থেকে উঠে এসেছে। কোভিডকালের আগেই ছিল নানা সঙ্কট। কোভিড ও দীর্ঘ লকডাউন তাকেই আরো মারাত্মক আকার দিয়েছে। এখন পশ্চিমবঙ্গে এরকম অসংখ্য সরকারী স্কুল আছে যেখানে ক্লাস এইটের ছেলেমেয়েদের অনেকেই ঠিকমত একটা পাঠ্যবই রিডিং পড়তে পারে না। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে সরকার বলে যাচ্ছেন শিক্ষার জন্য তারা কত কিছু করছেন। কন্যাশ্রী দিচ্ছেন, সবুজসাথী দিচ্ছেন, ট্যাবলেট/ স্মার্ট ফোন কেনার টাকা দিচ্ছেন, নানা স্কলারশিপ দিচ্ছেন, জামা কাপড় দিচ্ছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু মূল সমস্যাটা সমাধানের জন্য যে কিছুই করে উঠতে পারছেন না, সেইটে হল সবচেয়ে বড় খামতির জায়গা।
অথচ চাইলে যে সরকারী স্কুল শিক্ষার হাল ফেরানো যায়, সেটা দিল্লির কেজরিওয়াল সরকার করে দেখিয়েছেন। দেশের এক মেট্রো শহর দিল্লির সরকারী স্কুল শিক্ষা আর আর এক মেট্রো শহর কলকাতার সরকারী স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থার তুলনা করলে আকাশ পাতালের বিরাট ফারাক চোখে পড়বে। এই তুলনা এও দেখিয়ে দেয় যে চাইলে অনেক কাজ সরকার করেই উঠতে পারতেন। প্রাইমারি শিক্ষার হাল ফেরানোর কাজটা তারা তো ভালোভাবে শুরুই করলেন না। এখন দেখা যাচ্ছে আমরা যাদের হাতে রাজ্য শাসনের দায় তুলে দিয়েছিলাম, তারা শিক্ষাক্ষেত্রকে উন্নত করা নয়, তার থেকে কীভাবে টাকা কামানো যায় তাতেই মন প্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন। নিয়োগ দুর্নীতি ক কোটি টাকার কে জানে, কত দূর তার শিকড় বাকড় ছড়ানো তা নিয়ে নিত্যনতুন নানা খবর শোনাচ্ছে তদন্তকারী সংস্থাগুলো।
শিক্ষাবিদদের নয়, শিক্ষা নিয়ামক সংস্থাগুলির ঘরে এখন কেবল গোয়েন্দা পুলিশের যাতায়াত। শিক্ষাবিদেরা আলোচনাসভায় নয়, জেলের ভেতরে রয়েছেন তাদের পাপের শাস্তি নিয়ে। দুর্নীতির ফলে স্বাভাবিকভাবেই আদালতের দারস্থ হয়েছেন চাকুরী প্রার্থীরা। বন্ধ রয়েছে নতুন নিয়োগ। অসংখ্য স্কুল শিক্ষকের অভাবে ধুঁকছে। পড়াশুনো বন্ধ হবার মুখে। একটি দল ও তার কিছু মাতব্বর পশ্চিমবঙ্গের কোটি কোটি ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎটা একেবারে নষ্ট করে দিল। শুধু তাই নয় শিক্ষাব্যবস্থার মেরুদণ্ডকে এমনভাবে আঘাত করল, যে ঘুরে দাঁড়ানো হয়ে গেল খুব কঠিন।
এই অবস্থাকে চলতে দেওয়া যায় না। পশ্চিমবঙ্গে সরকারী কর্মচারী ও শিক্ষকদের যে জীবিকাগত ন্যায্য আন্দোলন চলছে, স্বচ্ছ নিয়োগের দাবি নিয়ে যে আন্দোলন চলছে, সেই সব জরুরী আন্দোলনের পাশাপাশি দরকার এক সামগ্রিক শিক্ষা আন্দোলন। যে আন্দোলন ভেঙে যাওয়া শিক্ষাব্যবস্থার হাল ফেরানোর কথাবলবে, সেই জন্য নাগরিক আন্দোলন তৈরির চেষ্টা করবে, শিক্ষা সংকটকে সমাজের সর্বস্তরে ‘টকিং পয়েন্ট’ করে তুলে সমস্যার সমাধান কীভাবে করা যায় – সেই চেষ্টা করবে। এই আন্দোলনকে কথা বলতে হবে ‘জাতীয় শিক্ষানীতি’ সংক্রান্ত বিষয় সহ আরো নানা কিছু নিয়ে। সেই সব বিষয় নিয়ে আমরা পরের কয়েকটি লেখায় ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করব।
- সৌভিক ঘোষাল