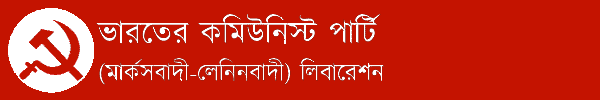গত ৮ জুলাই ২০২১, বিকেল পাঁচটা নাগাদ বাংলাদেশের রূপগঞ্জের কর্ণগোপ এলাকায় হাসেম ফুডের ছয়তলা এক কারখানা ভবনে আগুন লাগে। ফায়ার সার্ভিসের ১৮টি ইউনিট ২০ ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে পরদিন দুপুরে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এরপর ভবনের চতুর্থ তলা থেকে ৪৯ জন শ্রমিকের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। এর আগেই, আগুন লাগার পর ভবন থেকে লাফিয়ে পড়ে তিনজনের মৃত্যু হয়েছিল। ফায়ার সার্ভিসের আধিকারিকেরা জানিয়েছেন যে ওই কারখানায় প্লাস্টিক, ফয়েল, কাগজ, রেজিন, ঘি, প্রক্রিয়াজাত করা পণ্য ও নানা কেমিক্যালসহ প্রচুর দাহ্য পদার্থ ছিল। একারণে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে তাঁদের বেগ পেতে হয়।
জুস, ক্যান্ডি, বিস্কুট, লাচ্ছা সেমাইসহ বিভিন্ন খাদ্যপণ্য তৈরি হোতো হাসেম ফুডস লিমিটেডের কারখানায়। প্রায় পাঁচ হাজার শ্রমিক দিয়ে চলত তাদের কাজ। কর্মরত শিশু-কিশোর, শ্রমিক-জনতা পেটের আগুন জুড়ানোর জন্য মাত্র সপ্তাহখানেক আগে, ১ জুলাই ২০২১ রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করেছিলেন। দু’মাস ধরে তাঁদের বেতন ও ওভারটাইমের টাকা পরিশোধ করছিল না মালিকপক্ষ। বাড়িভাড়া ও মুদিদোকানের বকেয়া পরিশোধ করতে না পেরে বাধ্য হয়ে তাঁরা রাস্তায় নেমেছিলেন। সপ্তাহ না ঘুরতেই তাঁরা শিকার হলেন কারখানার রহস্যময় আগুনের।
১ জুলাই বিক্ষোভের খবর পেয়ে কাঁচপুর ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ ও ভুলতা ফাঁড়ি পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি ‘নিয়ন্ত্রণে’ এনেছিল। গলা উঁচু করে জানিয়ে গিয়েছিল, ‘মালিকপক্ষের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে। ৫ জুলাই শ্রমিকদের দুই মাসের বকেয়া ওভারটাইমের টাকা দিয়ে দেওয়া হবে। বাকিটা ঈদের আগে পরিশোধ করে দেওয়া হবে। কোম্পানির অ্যাডমিন ইনচার্জ ইঞ্জিনিয়ার সালাউদ্দিনও সংবাদমাধ্যমকে একই কথা বলেছিলেন। বলা বাহুল্য, কেউ কথা রাখেনি। পেটের আগুনে জ্বলতে জ্বলতে কারখানার আগুনে পুড়ে কয়লা হলেন তাঁরা।
অগ্নিকাণ্ডের ভয়াবহতা ব্যক্ত করে এক উদ্ধারকর্মী কাঁদতে কাঁদতে জানান, চেনা যায় না কে নারী কে পুরুষ, কোনটা মাথা, কোনটা হাত। মৃতদেহগুলো আগুনে পুড়ে এমন অবস্থা হয়েছে যে নারী, পুরুষ কিংবা পরিচয় — কারও পক্ষে কোনো কিছুই চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। বিক্ষুব্ধরা বলছেন, চারতলার ‘দরজা বন্ধ’ না থাকলে এত মৃত্যু হোত না। পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে, পাঁচ-ছয়তলায় কোনো লাশ মেলেনি। কিন্তু এটাকে অনেকেই বানানো কথা বলে মনে করেছেন। যেমন ঢাকা থেকে ছুটে যাওয়া সাংবাদিক ফারুক ওয়াসিফ। তাঁর মতে ‘এটা অসম্ভব’। নিচের সিঁড়ি আগুনে বন্ধ হওয়ায় সবাই ওপরে উঠে গিয়েছিল। ছাদের তালা খোলা না বন্ধ ছিল, জানা নেই। পাঁচ-ছয়তলায় অনেকের আটকা পড়ার কথা। তাঁদের লাশ কোথায় গেল? একটা হাজিরা খাতা পড়ে ছিল, পৃষ্ঠাগুলো ছেঁড়া।
তালা মারার অভিযোগ নিয়ে মালিকপক্ষ বিবিসিসহ বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছে, “এটি মিথ্যা কথা, এটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন”। প্রশ্ন উঠেছে তাহলে সত্য কোনটা? নাছোড়বান্দা এক তরুণ সাংবাদিক জানতে চান, তালা দেওয়া না থাকলে এতগুলো মৃতদেহ এক জায়গায় পাওয়া গেল কীভাবে? মালিকপক্ষের উত্তর, “যখন নিচতলায় আগুনটা ধরেছে, তখন সবাই আতঙ্কে ওপরে চলে গেছে”। তাই লোকগুলো পুড়ে কয়লা হয়েছে একসঙ্গে।
তাজরীন, রানা কি হা–মীম অথবা নরসিংদীর তোয়ালে কারখানা কিংবা গাজীপুরের চান্দনায় গরিব অ্যান্ড গরিব সোয়েটার কারখানা — বাংলাদেশ এরকম ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা একের পর এক দেখেই চলেছে। কিন্তু এই সমস্ত ঘটনাগুলি থেকে কোনও শিক্ষা নেওয়া হয়না। খরচ বাড়া ও মুনাফা কমার ভয়ে সুরক্ষা ব্যবস্থার দিকে মালিকপক্ষ বিন্দুমাত্র নজর দেয় না। পুলিশ প্রশাসনও এইসব দিনের পর দিন উপেক্ষা করে। গরীব মানুষ ভাত কাপড়ের টানে বাধ্য হয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিপদজনক পরিস্থিতিতে দিনের পর দিন সামান্য মজুরিতে কাজ করে যেতে বাধ্য হন। অগ্নিকাণ্ড ঘটলে সুরক্ষা ব্যবস্থার অভাবে পুড়ে কাঠকয়লা হয়ে যাওয়াই তাদের নিয়তি। বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নতি ও শিল্পবিকাশের যে ছবি বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়, তার ভেতরের মারাত্মক চেহারাটা এই সমস্ত ঘটনা থেকে বেরিয়ে আসে।

আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে যে শিশু কিশোর কিশোরীদের কাজ করানো হত, নারায়ণগঞ্জের ঘটনায় তা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। কিন্তু এই হতভাগ্য শিশু কিশোরদের সম্পূর্ণ তালিকা পাওয়াও বোধহয় সম্ভব হবে না কোনোদিনই। অপেক্ষমাণ অভিভাবক আর প্রাণে বেঁচে যাওয়া সহকর্মীদের কাছ থেকে যেসব নাবালক-নাবালিকার নাম পাওয়া গেছে, সেটাই এখন একমাত্র তালিকা। শান্তা (১২), মুন্না (১৪), শাহানা (১৫), নাজমুল (১৫), রিপন (১৭), তাকিয়া (১৪), হিমু (১৬), সুফিয়া (৩০), আমেনা (১৭), মাহমুদ (১৫), তাসলিমা (১৭), কম্পা (১৬) ছাড়াও আরও যে অনেক শিশু ছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাছাড়া যাদের বয়স ১৯-১৮ বলা হচ্ছে, যেমন শেফালি (২০), ইসমাইল (১৮), অমৃতা (১৯) — তাঁদের প্রকৃত বয়স নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তাঁদের সহকর্মীরা।
বাংলাদেশের প্রচলিত আইন শিশুদের কারখানা বা শিল্পপ্রতিষ্ঠানের শ্রমিক হিসেবে নিয়োগকে অনুমোদন করে না। আইনে বলা হয়েছে, “কোনো পেশায় বা প্রতিষ্ঠানে কোনো শিশুকে নিয়োগ করা যাবেনা বা কাজ করতে দেওয়া যাবেনা”। তবে শিশু আইনে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত সবাইকে শিশু বলা হলেও বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ অনুসারে ১৪ বছর বয়স পূর্ণ করেনি, এমন ব্যক্তিকেই ‘শিশু’ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। তবে কি ১৪ বছর পার হলেই সবাই প্রাপ্তবয়স্ক? না, তা নয়। শ্রম আইন প্রাপ্তবয়স্কের সুযোগ থেকে এই বয়সী মানুষদের বঞ্চিত রেখে তাঁদের কাছ থেকে সস্তা শ্রম কেনার একটা ব্যবস্থা করেছে। শ্রম আইন বলছে, “চৌদ্দ বৎসর বয়স পূর্ণ করিয়াছেন কিন্তু আঠারো বৎসর বয়স পূর্ণ করেন নাই, এমন কোনো ব্যক্তিকে ‘কিশোর’ হিসেবে গণ্য করা হইবে।” এদের কারখানায় শর্ত সাপেক্ষে নিয়োগ দেওয়া যাবে। কী সেই শর্ত?
শ্রম আইন ২০০৬ অনুসারে কিশোর শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে রেজিস্টার্ড চিকিৎসক কর্তৃক কিশোরকে প্রদত্ত সক্ষমতা প্রত্যয়নপত্র মালিকের হেফাজতে থাকতে হবে। কাজের নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ করে কিশোরের কর্ম-ঘণ্টা সম্পর্কে একটি নোটিশ প্রদর্শন করতে হবে।
তারপরও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার চাপেই হোক আর মুখরক্ষার জন্যই হোক, বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, প্রজ্ঞাপন (এসআরও নং ৬৫-আইন/২০১৩) জারির মাধ্যমে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজের একটা তালিকা তৈরি করে জানিয়ে দিয়েছিল সবাইকে। সেই তালিকায় যে ৩৮টি কাজে শিশু-কিশোরদের নিয়োগ না করার কথা বলা হয়েছিল, তার অন্তত চারটি লঙ্ঘন করার প্রমাণ মিলেছে এই কারখানায়। ৮ জুলাই যখন আগুন লাগে, তখন কিশোরদের জন্য নির্ধারিত পাঁচ কর্ম-ঘণ্টা যে অনেক আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।
এই অগ্নিকাণ্ড আবার সেই পুরোনো ক্ষতের দগদগে ঘাগুলো উন্মোচন করে দিয়েছে। নজরে আসছে নিয়মবহির্ভূত নির্মাণ, পরিদর্শন নেই, সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর উদাসীনতা ও প্রাতিষ্ঠানিক অব্যবস্থাপনা। একটি দুর্ঘটনা ঘটলে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো পরস্পরের সঙ্গে কুশল বিনিময় করে, অন্যথায় সহজে একত্র হয় না। সমন্বিত কোনো পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেনা। দুর্ঘটনার পর কয়েকটি কমিটি হয়। তারা কিছু সুপারিশ করে। কিন্তু সেসব সুপারিশ আদৌ বাস্তবায়িত হলো কিনা, এর ওপর কোনো নজরদারি থাকে না।
বাংলাদেশের যত্রতত্র ফায়ার সার্ভিস আর কারখানা পরিদর্শনের অনুমোদন ছাড়াই গড়ে উঠছে কলকারখানা, সম্প্রসারিত হচ্ছে তাদের বহুতল ভবন। এধরনের অব্যবস্থাপনার কারণেই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা বেড়ে চলেছে। কেউ জানেনা কে নিশ্চিত করবে অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে বিল্ডিং কোড মেনে নির্মাণের ব্যাপারে কার কতটা নজরদারি দরকার! ফায়ার সার্ভিসের অনুমোদন ছাড়া কোনো ভবনের কার্যক্রম শুরু করতে দেওয়া ঠিক হবে কি না? তাছাড়া কে কীভাবে নিশ্চিত করবে কলকারখানার জন্য উন্নত বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ব্যবহার ও নিয়মিত মেরামত করার কাজ, পর্যাপ্ত অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা রাখা ও কৃত্রিম জলাধার, ড্রামভর্তি জল সংরক্ষণ, প্রশস্ত সিঁড়ি ও বিকল্প জরুরি বহির্গমনের পথ রাখা, কর্মকালীন গেট বন্ধ না করা – সে সবও অনিশ্চিত!
অনেক দেশের মতো একসময় বাংলাদেশেও মোহিনী মিল, কেরু কোম্পানি, চিত্তরঞ্জন বস্ত্র মিল, এমনকি আদমজীতেও শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনা যৌথ নিরাপত্তা কমিটি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এসব কাজ করত। নিশ্চিত করত শ্রমিকদের আর কারখানার নিরাপত্তা। দেখত সিঁড়িঘরে বা যত্রতত্র মালামাল না রেখে আলাদা গুদামে সংরক্ষণ হচ্ছে কিনা, নিরাপত্তা প্রহরীর জন্য বিশেষ জরুরি টেলিফোন ব্যবস্থাসহ বিদ্যুৎ বিভাগ ও ফায়ার সার্ভিসের টেলিফোন নম্বর শ্রমিকেরা জানেন কিনা। কারখানায় প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সহ শ্রমিকদের অগ্নিনির্বাপণের প্রশিক্ষণ প্রদানের কাজ হচ্ছে কিনা।
আসলে আইন মানার সংস্কৃতি আর জবাবদিহি না থাকলে মানুষ মরবে, শিশুদের লাশের হিসাব মিলবে না, এ আর নতুন কী!
(সূত্র: বিভিন্ন সংবাদপত্রের রিপোর্ট)