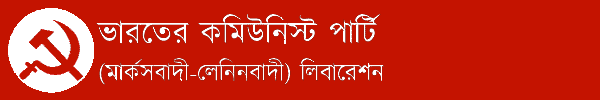ফ্যাসিবাদের আগ্রাসী চরিত্র নিহিত থাকে তাদের যুদ্ধ বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গির অন্তর্বস্তুতে। তারা যুদ্ধকে সবচাইতে বেশি গুরুত্ব দেয় এবং এই যুদ্ধের মধ্যে দিয়েই প্রতিবাদ কিম্বা প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করে তাদের আধিপত্য কায়েম করতে চায়। বেনিতো মুসোলিনি তো কোনরকম দ্বিধাব্যতিরেকেই বলেছিলেন, ‘থ্রি চিয়ার্সফর দ্য ওঅর’! তিনি ইতালির যা কিছু মহৎ এবং সুন্দর তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের কামান দাগতে চেয়েছিলেন! তিনি ছিলেন সর্বাত্মক যুদ্ধের পক্ষপাতী। অন্যত্র আবার তিনি বলেছিলেন যে ‘শান্তি’ হছে অবাস্তবের শিল্পচর্চা, প্রকৃতপক্ষে শান্তি হচ্ছে যুদ্ধের আপাত-বিরতি!
আমাদের দেশে ফ্যাসিবাদের প্রবক্তা এবং অনুশীলক বিজেপি-আরএসএস এই যুদ্ধকে সবসময় জারি রেখে তাদের উদ্দেশ্য সাধনের পথকে বেছে নিয়েছে। তাদের বিবেচনায় যুক্তির ওপরে হৃদয়কে স্থান দিতে হবে। অর্থাৎ যুক্তিদ্রোহিতার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ভাবাবেগ- তাড়িত কোমল হৃদয়কে তারা ব্যবহার করতে চায় এই যুদ্ধের উপকরণ হিসেবে। স্বভাবতই দেশের সংখ্যালঘু মুসলিম, দলিত, ক্রিশ্চিয়ান সহ অহিন্দুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জারি রাখতেই তারা তাদের কর্মসূচিকে সক্রিয় করে তোলে। মুসলিম বিরোধিতাকে তাদের আশু কর্মসূচির শীর্ষেস্থান দেয়। প্রতিবাদকে মুসলিম দেশ পাকিস্তানের স্বার্থসম্পূরক বলে দাগা দিয়ে দেয়! ফ্যাসিবাদের সব চাইতে বড় শত্রু ছিল কমিউনিজম। এই কমিউনিস্ট নেতা কমরেড স্তালিনের নেতৃত্বে লাল ফৌজের কাছে শেষপর্যন্ত হিটলারের নেতৃত্বে ফ্যাসিবাদের চুড়ান্ত পরাজয় ঘটেছিল। কমিউনিস্টদের হাতে তাদের এই পরাজয়কে ফ্যাসিস্তরা কখনও মন থেকে মেনে নিতে পারেনি। আমাদের দেশের এই ফ্যাসিস্ত মতাদর্শের ফেরিঅলারা এই মতাদর্শের মধ্যে সর্বদাই আশঙ্কার ঘনায়মান সিঁদুরে মেঘ দেখে থাকে। সুতরাং তারা ঘোষিতভাবেই মার্কসবাদ এবং কমিউনিজমের ঘোরতর শত্রু। নকশালপন্থী তথা মাওবাদীদের তারা তাদের জাতশত্রু হিসেবেই গণ্য করে থাকে। এঁদের নেতৃত্বে সংগঠিত আন্দোলন দমনে কতটা নির্মম এরা হতে পারে তার নিদর্শন আমাদের দেশের বিভিন্ন নকশাল-মাওবাদী অধ্যুষিত লড়াইয়ের অধিক্ষেত্রগুলিতে তার জ্বলন্ত সাক্ষ্য বর্তমান।
এই যাদের রাজনৈতিক দর্শন, তারা স্বভাবতই তাদের অভিপ্রায় সাধনের লক্ষ্যে ভাবাবেগ নির্মাণের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে যুক্তিকে পেছনের দরজা দিয়ে নির্বাসন দিয়ে থাকে। যারাই তাদের হিন্দুত্বের পক্ষে অতীতে কিছুমাত্র ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছেন, তারা তাদের কাছে গ্রহণীয় বীর, পূজনীয় নেতৃত্ব, বরণীয় পুরুষ হিসেবে আখ্যাত হন। আর যারা সমাজেতিহাসে এর বিপ্রতীপ ভূমিকা পালন করেছেন তাঁরা তাদের কাছে তাদের অবলম্বিত হিন্দুত্বের শত্রু! আর তাদের এই ফ্যাসিবাদিক ‘হিন্দুত্ব’ রক্ষার কারণে তারা অবৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনাকে একদিকে যেমন মান্যতা দেয়, বিজ্ঞানকে তাদের ফ্যাসিবাদী ধর্মতত্ত্বের আধারে জারিত করে, তেমনি পাশাপাশি সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধকে নতুনভাবে কায়েম করে ইতিহাসের চাকা পেছন দিকে ফেরাবার চেষ্টায় নিয়োজিত থাকে। এর ফলে দেখা যায় অতীতকালের নিন্দিত সামাজিক কুপ্রথাগুলিকে তারা এখন আবার নতুন করে সামাজিক অনুমোদন দিতে উদ্যোগী হয়েছে! রাজস্থানের ‘জহরব্রত’, বাংলার ‘সতীদাহ’, ‘বিধবাবিবাহ’ বিরোধিতা প্রমুখ সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রায়োগিক অনুশীলনের বিষয়গুলিকে তারা আবার নতুন করে অনুমোদন দিতে পুরানো সমাজের পুনঃপ্রবর্তন চাইছে! বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা প্রমুখ হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষা এবং অনুশাসনের মধ্যে থেকে তারা তাদের উপকরণ সংগ্রহ করে হিন্দু ভাবাবেগে জোয়ার আনার উদ্যোগ নিয়েছে। আর এই জোয়ারে ভেসে যাচ্ছে যুক্তি, বিজ্ঞানের প্রতিপক্ষতা!
রামচন্দ্র হয়ে উঠেছেন উদ্যোগ-পুরুষ! তাঁর ভক্ত হনুমান হয়ে উঠেছে আরাধ্য দেবতা! রামচন্দ্রের পাশাপাশি হনুমানেরও মন্দির গজিয়ে উঠেছে, সেখানে নবভক্তেরা ভিড় জমাচ্ছেন! চলছে পূজার্চনা! উৎখাত হচ্ছে মসজিদ, না হলেও উৎখাতের প্রয়াস জারি আছে। রামমন্দির নির্মাণ করতেই হবে! প্রয়োজনে জবরদস্তিও চলবে। প্রয়োজনে দাঙ্গাও। মন্দির সংস্কৃতিই তো সামন্ত সংস্কৃতি টিকিয়ে রাখার একটি প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়াস।
ঊনিশ শতকে রামমোহন যখন এই কুৎসিত এবং অমানবিক সতীদাহ প্রথা বিলোপের লক্ষ্যে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, তখন বিদ্যাসাগর নিতান্তই কিশোর। ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে আইন করে যখন লর্ড বেন্টিঙ্ক এই সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করেন, তখনও বিদ্যাসাগরের বয়স দশের নীচে। রামমোহন সতীপ্রথার অবসানের লক্ষ্যে আন্দোলনে সামিল হলে সমসময়ের হিন্দু সমাজের রক্ষণশীলরা রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে প্রতি-আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন। তবে মনে রাখা দরকার যে সতীদাহ নিবর্তকের যুক্তির ক্ষেত্রে রামমোহন কিন্তু ‘মনুসংহিতাকে প্রমাণ’ হিসেবে মান্যতা দিয়েছিলেন! তাঁর বিবেচনায় সহমরণের বিপ্রতীপে আজীবন ব্রহ্মচর্য পালন কর্মকে রামমোহন ‘শাস্ত্রসিদ্ধ’ বলে মনে করতেন! একজন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক জানিয়েছেন যে বেন্টিঙ্ক যখন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধকরণের প্রয়াস নেন, তখন রামমোহন আপত্তি করেছিলেন। কারণ তিনি চেয়েছিলেন আইন করে নয়, সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচারের মাধ্যমেই এই কুপ্রথার অবসান ঘটবে! অবশ্য বেন্টিঙ্ক আইন করে এই কুপ্রথা নিষিদ্ধ করার পর রামমোহন সদলবলে গিয়ে বেন্টিঙ্ককে অভিনন্দন জানিয়ে এসেছিলেন।
সমসময়ে যারা এই কুপ্রথার সপক্ষতা করেছিলেন তারা তখনকার সমাজের হিন্দুত্বের অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্কমালা। এঁরা এই সতীপ্রথা নিষিদ্ধ হওয়ার আগে এবং অব্যবহিত পরেও তাঁদের তীব্র বিরোধিতা জারি রেখেছিলেন। তাঁদের সেই জারি রাখা যুদ্ধের মশাল আজ আবার আমাদের দেশের হিন্দুত্ববাদী ফ্যাসিস্তরা হাতে তুলে নিয়ে সতীপ্রথার সপক্ষতা করছেন! অন্যদিকে বিদ্যাসাগর নারীজাতির দুঃখকষ্ট শৈশবকাল থেকেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। স্বভাবতই নারীমুক্তির আধুনিক চিন্তার সঙ্গে তাঁর পরিচিতি না ঘটলেও তিনি তাঁর মতো করে আমাদের দেশের নারীজাতির সামাজিক মুক্তির বিষয়ে ভাবিত হয়ে তার অনুশীলনব্রতে দীক্ষিত হয়েছিলেন। এক্ষেত্রেও তাঁর লড়াইয়ের হাতিয়ার ছিল প্রচলিত শাস্ত্রীয় যুক্তি। এই শাস্ত্রীয় যুক্তির ব্যাখ্যার মধ্যেই তিনি সমস্যার সমাধান সন্ধান করেছিলেন!
ব্রাহ্মনেতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে রক্ষণশীল হিন্দুনেতা রাজা রাধাকান্ত দেবের ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রে অনেকটা মতৈক্য লক্ষ্য করা যায়। একটা সময় রাধাকান্ত দেব তো দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্ববোধিনী সভার সদস্যও ছিলেন! তবে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোদ্ধা বিদ্যাসাগর দেবেন্দ্রনাথের মতের শরিক হননি। তাঁরা তো একটা সময় দেবেন্দ্রনাথের নিকট ‘নাস্তিক’ বলে আখ্যাত হয়েছিলেন। আবার অক্ষয়কুমার দত্তের মতো সমসময়ের প্রখর যুক্তিবাদী ব্যক্তিত্বও জাতিভেদ প্রথার আশু বিলোপের ব্যাপারে সহমত হননি! উনিশ শতক ছিল এমনই বিরোধপুঞ্জিত এক আশ্চর্য সময়। স্ববিরোধিতা ছিলো যে সমসময়ের কালধর্ম, অঙ্গভূষণ।
রামমোহন সতীপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করলেও বিধবাবিবাহ নিয়ে তাঁর চিন্তা অনুকূল ছিল না, বরং বিপরীত ছিল। অন্যদিকেবিদ্যাসাগর যখন বিধবাবিবাহের বিষয়ে আন্দোলনে নামেন, তখনও তাঁর প্রতিপক্ষতা করতে এগিয়ে এসেছিলেন সেই হিন্দু রক্ষণশীলরা। তাঁদের প্রবল প্রতিপক্ষতার মোকাবিলা করেই বিদ্যাসাগর এই আন্দোলনে সাফল্য অর্জন করেছিলেন। তিনি যে মানবিকতার প্রশ্নটিকে কত গভীরতা থেকে বিধবাবিবাহের ক্ষেত্রে দেখেছিলেন তা তাঁর ‘বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিৎ কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব’-এর দ্বিতীয় পুস্তকে নিহিত আছে। এখানে তিনি লিখেছিলেন, ‘তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই স্ত্রীজাতির শরীর লৌহময় হয়? ক্ষুধা বলিয়া বোধ হয় না? তৃষ্ণা বলিয়া বোধ হয় না? দুর্জয় রিপুবর্গ এক কালে নির্মূল হইয়া যায়?’ ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি স্মৃতিশাস্ত্র অনুসন্ধান করে পরাশরের একটি শ্লোকের সন্ধান পান যা তাঁর এই আন্দোলনের যুক্তিভিত্তি নির্মাণ করেছিল। এই শ্লোক অনুযায়ী স্বামী নিরুদ্দিষ্ট, প্রয়াত, প্রব্রজ্যাগ্রহণকারী, ক্লীব কিম্বা পতিত হলে নারীর পক্ষে অন্য পতি গ্রহণ যথার্থ। এই বক্তব্যই বিদ্যাসাগরের যৌক্তিক হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল। এই আন্দোলনে সামিল হয়ে সমসময়ে বিদ্যাসাগর একদিকে যেমন প্রচুর কুৎসার মোকাবিলা করেছিলেন, তেমনই ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণের শিকারও হয়েছিলেন। এমনকি কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তও বিদ্যাসাগরের বিরোধিতায় সামিল হয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর এক উপন্যাসে এক চরিত্রের মুখ দিয়ে বলিয়েছিলেন, ‘বিধবার যে বিয়ে দেয়, সে যদি পণ্ডিত তবে মূর্খকে?’
অবশেষে সরকারি আনুকূল্যে বিধবাবিবাহ আইনসম্মত হওয়ার প্রায় বছর খানেক পরও কোনও বিধবাবিবাহের ঘটনা ঘটেনি। তখন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যাসাগরকে আবার ব্যঙ্গ করে লিখেছিলেন, ‘মুখে বলা বলা নয় কাজে করা করা।’ শেষপর্যন্ত ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের ৭ ডিসেম্বর এই আইনানুসারে প্রথম বিধবাবিবাহ সংঘটিত হয়। এরপর ক্রমান্বয়ে বিধবাবিবাহ সংঘটিত হতে থাকে। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে নিজের পুত্র নারায়নচন্দ্রের বিধবাবিবাহের ঘটনাকে কেন্দ্র করে নিজের স্ত্রী এবং আত্মীয়স্বজনের তীব্র বিরোধিতার মোকাবিলাও বিদ্যাসাগরকে করতে হয়েছিল। তবু ‘আপনি আচরি ধর্ম’ তিনি অপরকে শেখাতে ব্রতী হয়েছিলেন
সেই সময়ের হিন্দু রক্ষণশীলদের সেদিনের হাতিয়ার আজ আবার তুলে নিয়েছে অধুনা হিন্দুত্ববাদী ফ্যাসিস্তরা। বিদ্যাসাগরের মতো এই ‘হিন্দুস্বার্থ’ বিরোধীর মূর্তিভেঙে কি তারা আজ নতুন করে বার্তা দিতে চেয়েছে? উনিশ শতকে কোনও ধর্মধ্বজীদের আনুকূল্য ব্যতিরেকে এমন সামাজিক বিপ্লবী আন্দোলনের সংগঠক বিদ্যাসাগর তো স্বাভাবিকভাবেই হিন্দুত্ববাদী ফ্যাসিস্তদের চোখে অমার্জনীয় শত্রু হিসবে গণ্য হবেনই। তাই কি তারা গত ১৪ মে বিজেপি নেতা অমিত শাহের কলকাতায় নির্বাচনী প্রচারে রোড শো’র সময় বিদ্যাসাগর কলেজের বিদ্যাসাগরের মূর্তিটি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে? বিদ্যাসাগর দেশাচারের ‘দাস’ ছিলেন না, অথচ এই ফ্যাসিস্ত হিন্দুত্ববাদীরা দেশাচারকে প্রতিষ্ঠা দিয়ে তাকে ‘জনগ্রাহ্য’ করে সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধকে উজ্জীবিত করতে চায়। তাদের কাছে রূপ কানোয়ারকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা মহান হিন্দুধর্মীয় নজির! রাজস্থানের শিকার জেলার দেওরালা গ্রামে ১৯৮৭-র ৪ সেপ্টেম্বর মৃত স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় ১৮ বছর বয়সি রূপ কানোয়ারকে পুড়িয়ে হত্যা করে হিন্দুত্ববাদীরা। আর তার এই মৃত্যুকে গৌরাবান্বিত করে রূপকে ‘সতীমাতা’র মাহাত্ম্য দান করা হয়েছিল! এই হত্যার মদতদাতা এগারো জন রাজনৈতিক নেতাকে গ্রেপ্তার করা হলেও আদালতের আদেশে তাঁরা সবাই মুক্তি পেয়েছিলেন! ‘দ্য ওয়াল’ পরিবেশিত গত জানুয়ারি মাসের এক সংবাদে জানা যায় যে উত্তরপ্রদেশের বান্দা জেলার বারকোলা গ্রামে পঁচাত্তর বছর বয়সি এক মহিলাকে তাঁর মৃত স্বামীর চিতায় সহমৃতা হওয়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু পুলিশের সময়োচিত পদক্ষেপে তা আর সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এই হিন্দুত্ববাদীরা এইসব পুরানো কুসংস্কারগুলোকে নতুনভাবে আবার প্রতিষ্ঠা দিয়ে ‘সতী’মায়ের মাহাত্ম্য কীর্তন করে সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের পুনর্জাগরণ চাইছে তাদের হিন্দুত্ববাদী ফ্যাসিস্ত রাজনীতির উজ্জীবনের স্বার্থেই। স্বভাবতই সেকালের রাধাকান্ত দেবদের ঠিকা এখন নিয়েছেন এই সব হিন্দুত্ববাদীরা এবং উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁরা এখন রাধাকান্তদের ব্যাটন হাতে নিয়ে রামমোহন-বিদ্যাসাগর প্রমুখের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করবে এতে আর আশ্চর্য কি? বিদ্যাসাগর কলেজে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া তো তাদের এই রাজনৈতিক বোধসঞ্জাত প্রায়োগিকতা। তারা যেমন তাদের জাতশত্রু লেনিনের মূর্তি ভাঙে, পেরিয়ারের মূর্তি ভাঙে, আম্বেদকরের মূর্তি ভাঙে, তেমনই ভাঙে বিদ্যাসাগরের মূর্তিও। কেননা মধ্যযুগীয় কুসংস্কারের বিরোধিতা, বিজ্ঞানমনস্কতা তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে। উল্টোদিকে তারা মূর্তিগড়ে এই ফ্যাসিস্ত রাজনীতির পুরোধাদের। তাই তারা নির্মাণ করে নাথুরাম গডসের মূর্তি। একদিকে তারা যেমন আমদানি করে ভাঙনের সংস্কৃতি, তেমন অন্যদিকে প্রতিষ্ঠা করে ফ্যাসিস্ত নায়কদের মূর্তি!
এভাবেই এই হিন্দুত্ববাদী ফ্যাসিস্তরা তাদের রাজনৈতিক অভিযাত্রার স্বার্থেই এক সর্বাত্মক যুদ্ধ জারি রাখতে চায়। যা কিছু তাদের স্বার্থের প্রতিকূল তা তারা ধ্বংস করতে চায়, নির্মাণ করতে চায় কেবলমাত্র যা তাদের স্বার্থের অনুকূল। হিটলার-মুসোলিনির এই অন্ধ অনুগামীরা সর্বদাই যুদ্ধের পক্ষে ‘থ্রি চিয়ার্স’ ধ্বনি দেয়। এদেশের, বিশেষত বাংলাদেশের, যা কিছু সুন্দর, মহৎ তার বিরুদ্ধে তারা কামান দাগতে চায়। এদের আচার-ব্যবহার, চাল-চলনে, চলনে-বলনে সব সময়ই এক সর্বাত্মক যুদ্ধের আওয়াজ। এখন ‘জয় শ্রীরাম’ হয়ে উঠেছে তাদের ‘লিঞ্চিং ক্রাই’। প্রতিবাদীকে হত্যা করার সময় তারা স্লোগান দেয় ‘জয় শ্রীরাম’, ধর্ষণ করে হত্যার সময় ধ্বনি দেয় ‘জয় শ্রীরাম’, দাঙ্গা এবং লুট করার সময়ও অচিরেই এই ধ্বনি ক্রমাগত প্রতিধ্বনিত হবে ‘জয় শ্রীরাম’! দ্বিতীয়বার ক্ষমতার তখতে বসার পর এখন তারা সারা দেশ জুড়ে, বিশেষত আমাদের পশ্চিমবাংলা জুড়ে এক যুদ্ধাত্মক অস্থিরতার জন্ম দিয়েছে। শান্তি তাদের কাছে অবাস্তবের শিল্পচর্চা! তাদের কাছে শান্তির অর্থ যুদ্ধের বিরতি, যা তাদের কাছে একান্তই অনাকাঙ্ক্ষিত। এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে আর এক যুদ্ধের প্রস্তুতির দিন এসে গিয়েছে।
এই যুদ্ধে বিপ্লবী সাংস্কৃতিক কর্মীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এই যুদ্ধের সঙ্গীত তথা রণসঙ্গীত (ওঅর ক্রাই) রচনার দায়িত্ব তাঁদের ওপরই বর্তায়। এই সন্ধিকালের ইতিহাস উন্মুখ চোখে তাকিয়ে আছে তাঁদের দিকে।